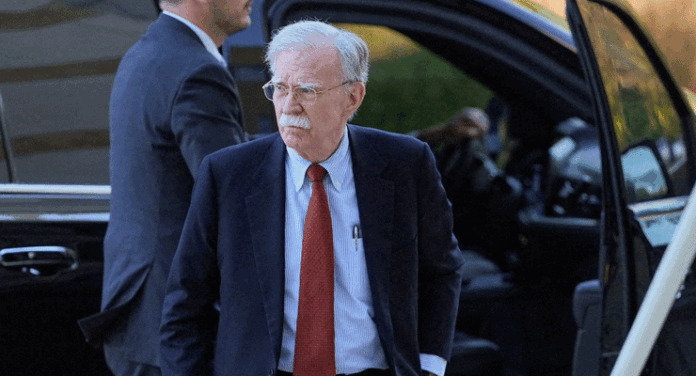মার্কিন রাজনীতিতে আবারও শুরু হয়েছে ক্ষমতা ও আইনের ভারসাম্য নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক। যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্টের পদে থাকা ব্যক্তির ক্ষমতা কতদূর যেতে পারে—এই প্রশ্ন এখন নতুনভাবে সামনে এসেছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় ফেরার পর। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিচারব্যবস্থাকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার অভিযোগে দেশজুড়ে উঠেছে উদ্বেগের ঢেউ।
ট্রাম্প তাঁর এক পোস্টে লিখেছেন, “যে ব্যক্তি তার দেশকে রক্ষা করে, সে কোনো আইন ভঙ্গ করে না।” এই বক্তব্যটিই যেন তাঁর নতুন নীতির প্রতিচ্ছবি—যেখানে প্রেসিডেন্টের পদকে গণতন্ত্রের সীমারেখার বাইরে এক প্রকার ‘রাজকীয় ক্ষমতা’ হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালতের সাম্প্রতিক এক রায় প্রেসিডেন্টকে কার্যত আইনি দায়মুক্তি দিয়েছে বলে অনেকেই মনে করছেন। এর ফলেই ট্রাম্প আরও দৃঢ় হয়েছেন, আর এই ‘অসীম ক্ষমতা’ নিয়েই তিনি এগোচ্ছেন।
দেশজুড়ে “No Kings” নামে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে সাধারণ মানুষ, যারা প্রেসিডেন্টের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে শনিবার দেশজুড়ে রাস্তায় নামছে। জাতীয় নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ ও সাবেক গোয়েন্দা কর্মকর্তারা সতর্ক করে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে যেখানে নির্বাচন ও আদালত টিকে থাকলেও সেগুলো কার্যত নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণে চলে যাচ্ছে—অর্থাৎ এক ধরনের competitive authoritarianism-এর দিকে যাচ্ছে দেশটি।
বিচারব্যবস্থা গণতন্ত্রের ভিত্তি—এই বিশ্বাসকেই এখন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছেন ট্রাম্প। আদালতের রায় উপেক্ষা, জানুয়ারি ৬–এর দাঙ্গায় অংশ নেওয়া দোষীদের ক্ষমা, বিচার বিভাগে নিজস্ব লোক বসানো এবং রাজনৈতিক প্রতিশোধের হাতিয়ার হিসেবে আইনকে ব্যবহার—সব মিলিয়ে আইনের শাসন এখন ‘আইনের অপব্যবহারে’ রূপ নিচ্ছে।
সম্প্রতি সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বোল্টন–এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে গোপন নথি ব্যবহারের মামলায়। মাত্র এক মাসের ব্যবধানে এটি ট্রাম্প প্রশাসনের তৃতীয় উচ্চপ্রোফাইল ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা। এর আগে নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল জেমস–এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় মর্টগেজ জালিয়াতির, আর সাবেক এফবিআই পরিচালক কমি–এর বিরুদ্ধে কংগ্রেসে মিথ্যা বিবৃতির অভিযোগ তোলা হয়। তিনজনই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।
এদিকে এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ট্রাম্প নিজের প্রতিহিংসার ভাবনা প্রকাশ করে ফেলেন, যেখানে তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, “তারা আমাকে দু’বার ইমপিচ করেছে, পাঁচবার মামলা করেছে, কিছুই প্রমাণ করতে পারেনি। এবার ন্যায়বিচার চাই—এখনই!”
যদিও বোল্টনের মামলাটি কিছুটা আলাদা। এই মামলা শুরু হয়েছিল বাইডেন প্রশাসনের সময়ে এবং একজন পেশাদার প্রসিকিউটরের অনুমোদনেই চার্জ গঠন হয়। কিন্তু এদিকে প্রতিরক্ষা সচিব হেগসেথ–এর বিরুদ্ধে সামরিক গোপন তথ্য ফাঁসের অভিযোগে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন।
ট্রাম্প অতীতেও বোল্টনের প্রতি প্রকাশ্যে বিদ্বেষ দেখিয়েছেন, এমনকি তাঁর নিরাপত্তা দলকেও সরিয়ে দিয়েছিলেন। বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কারাগারে পাঠানোর আহ্বান, এমনকি বিচারকদের বিরুদ্ধেও মন্তব্য—সব মিলিয়ে এক ভয়াবহ নজির তৈরি হয়েছে।
নিজের রাজনৈতিক প্রতিহিংসাকে ট্রাম্প এখন “জনগণের ন্যায়বিচার” হিসেবে বিক্রি করছেন। তাঁর প্রচারণার স্লোগানই বলছে—“I am your retribution”। সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, এক-তৃতীয়াংশ রিপাবলিকান সমর্থক মনে করেন, যারা প্রেসিডেন্টের বিরোধিতা করবে তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করা উচিত।
শনিবারের প্রতিবাদকে ট্রাম্প প্রশাসন ইতিমধ্যে “রাষ্ট্রবিরোধী” কর্মকাণ্ড হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। ক্ষমতায় টিকে থাকার কৌশল হিসেবে তিনি বারবার সঙ্কট সৃষ্টি করে গণতন্ত্রের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে আড়াল করছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটাই গণতন্ত্রের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ—যখন আইন হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত প্রতিশোধের অস্ত্র।
এই বাস্তবতায় অনেকেই বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র এখন ‘rule of law’ থেকে সরে গিয়ে ‘rule by law’-এর দিকে যাচ্ছে—অর্থাৎ, আইন আর শাসকের নিয়ন্ত্রণে পরিণত হচ্ছে, যা গণতন্ত্রের জন্য এক অশুভ ইঙ্গিত।