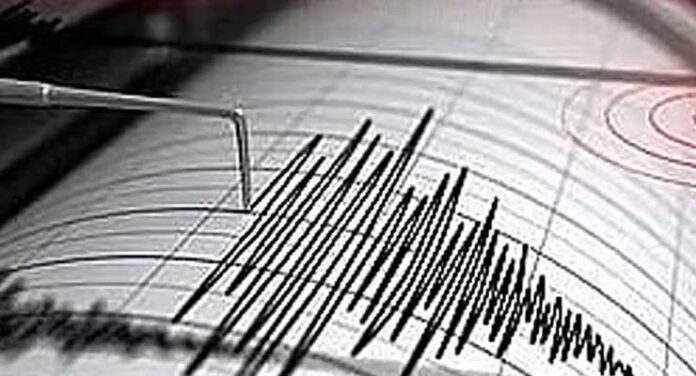পৃথিবীর ভেতরে দুটি ভূপৃষ্ঠ ব্লক হঠাৎ একে অপরের পাশ দিয়ে সরে গেলে যে কম্পন অনুভূত হয়, সেটিই ভূমিকম্প। এই সরে যাওয়া যে তলের বরাবর ঘটে, তা পরিচিত চ্যুতিতল নামে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে নির্দিষ্ট স্থান থেকে কম্পনের উৎপত্তি ঘটে, তাকে বলা হয় ভূমিকম্পের কেন্দ্র বা হাইপোসেন্টার। আর এর ঠিক ওপরের ভূপৃষ্ঠের বিন্দুটি পরিচিত উপকেন্দ্র হিসেবে।
বেশ কিছু ক্ষেত্রে বড় ভূমিকম্পের আগে ছোট কম্পন অনুভূত হয়, যাকে বলা হয় পূর্বাভাস কম্পন। এগুলো সাধারণত একই অঞ্চলে ঘটে, যেখানে পরবর্তী মূল ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। বড় কম্পনকে মূল কম্পন হিসেবে ধরা হয় এবং এর পরবর্তী সময়ে একই স্থানে ছোট ছোট কম্পন পুনরায় দেখা যায়, যেগুলো আফটারশক নামে পরিচিত। মূল কম্পনের মাত্রার ওপর নির্ভর করে আফটারশক কয়েক সপ্তাহ এমনকি কয়েক মাস ধরে চলতে পারে।
পৃথিবীর অভ্যন্তর চারটি স্তরে বিভক্ত। অন্তঃস্থ কেন্দ্র, বহিস্থ কেন্দ্র, ম্যান্টল ও ভূত্বক। ভূত্বক এবং ম্যান্টলের উপরের অংশ মিলেই পৃথিবীর পৃষ্ঠে একটি পাতলা স্তর তৈরি করে, যা আসলে অগণিত টেকটোনিক প্লেটে বিভক্ত। এই প্লেটগুলো এককভাবে স্থির নয়, বরং ধীরে ধীরে নড়াচড়া করে এবং পরস্পরের সীমানায় ঘর্ষণ তৈরি করে। এই সীমানাগুলোকে প্লেট বাউন্ডারি বলা হয়, যেগুলোতে অসংখ্য চ্যুতি থাকে। বিশ্বজুড়ে অধিকাংশ ভূমিকম্প ঘটে এই চ্যুতিগুলোর ভেতরে। প্লেটের রুক্ষ কিনারা পরস্পরের সঙ্গে আটকে থাকলেও প্লেটের বাকি অংশ নড়তে থাকে। যখন আটকে থাকা অংশ অতিরিক্ত চাপ সহ্য করতে না পেরে আলাদা হয়ে যায়, তখনই ঘটে ভূমিকম্প।
ভূমিকম্পের সময় কেন পৃথিবী কেঁপে ওঠে তা বুঝতে হলে সঞ্চিত শক্তির মুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া লক্ষ্য করতে হয়। চ্যুতির কিনারা আটকে থাকার সময় শক্তি জমা হতে থাকে। যখন চলমান ব্লকের বল এই ঘর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম করে, তখন হঠাৎ করে সঞ্চিত শক্তি ভূকম্পন তরঙ্গ আকারে ছড়িয়ে পড়ে। এই তরঙ্গগুলো পুকুরে ঢেউয়ের মতো সবদিকে ছুটে যায় এবং পৃথিবীপৃষ্ঠে পৌঁছে মাটি ও স্থাপনা কাঁপিয়ে তোলে।
ভূমিকম্প রেকর্ড করার জন্য ব্যবহৃত হয় সিসমোগ্রাফ। এই যন্ত্রের নিচের অংশ মাটির সঙ্গে স্থিরভাবে যুক্ত থাকে, আর একটি ভারী অংশ মুক্তভাবে ঝুলে থাকে। ভূমিকম্পের সময় মাটি কেঁপে ওঠে, ফলে সিসমোগ্রাফের ভিত্তি দুললেও ঝুলে থাকা ভার প্রায় স্থির থাকে। দুটি অংশের এই অবস্থানগত পার্থক্য রেখাচিত্র হিসেবে সিসমোগ্রামে রেকর্ড হয়।
ভূমিকম্পের মাত্রা বা ম্যাগনিচিউড নির্ধারণ করা হয় চ্যুতির আকার এবং চ্যুতির ওপর পিছলে যাওয়ার পরিমাণ বিশ্লেষণ করে। যেহেতু এসব চ্যুতি গভীর ভূগর্ভে থাকে, তাই মাপার যন্ত্র দিয়ে সরাসরি পরিমাপ করা সম্ভব নয়। সিসমোগ্রাম বিশ্লেষণের মাধ্যমেই বিজ্ঞানীরা ছোট ও বড় ভূমিকম্পের পার্থক্য নির্ণয় করেন। সংক্ষিপ্ত, কম নড়াচড়ার রেখা মানে ছোট ভূমিকম্প এবং দীর্ঘ, তীব্র নড়াচড়া মানে বড় ভূমিকম্প।
ভূমিকম্পের অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও পি ও এস তরঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পি তরঙ্গ দ্রুতগামী, এস তরঙ্গ তুলনামূলক ধীর। বজ্রপাতের আলো ও শব্দের পার্থক্যের মতো পি ও এস তরঙ্গের সময় ব্যবধান বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা নির্ণয় করেন ভূমিকম্প কেন্দ্র কত দূরে ছিল। তবে একক সিসমোগ্রাফ দিয়ে দিক নির্ণয় করা যায় না। এজন্যই ট্রায়াঙ্গুলেশন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। তিনটি ভিন্ন সিসমোগ্রাফ স্টেশনের রেকর্ড অনুযায়ী দূরত্ব নির্ধারণ করে মানচিত্রে তিনটি বৃত্ত আঁকা হয় এবং যেখানে তিনটি বৃত্ত মিলিত হয়, সেখানেই উপকেন্দ্র।
এখনও পর্যন্ত ভূমিকম্পের সুনির্দিষ্ট পূর্বাভাস দেওয়ার কার্যকর কোনো পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়নি। বিজ্ঞানীরা জানেন নির্দিষ্ট চ্যুতিতে ভবিষ্যতে আরও কম্পন ঘটবে, কিন্তু ঠিক কখন তা ঘটবে তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এই অনিশ্চয়তার কারণেই ভূমিকম্প মানুষের কাছে অন্যতম অনির্দেশ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে বিবেচিত।